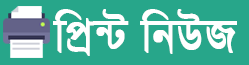বিখ্যাত গাড়ির ব্র্যান্ডগুলো এল কোত্থেকে
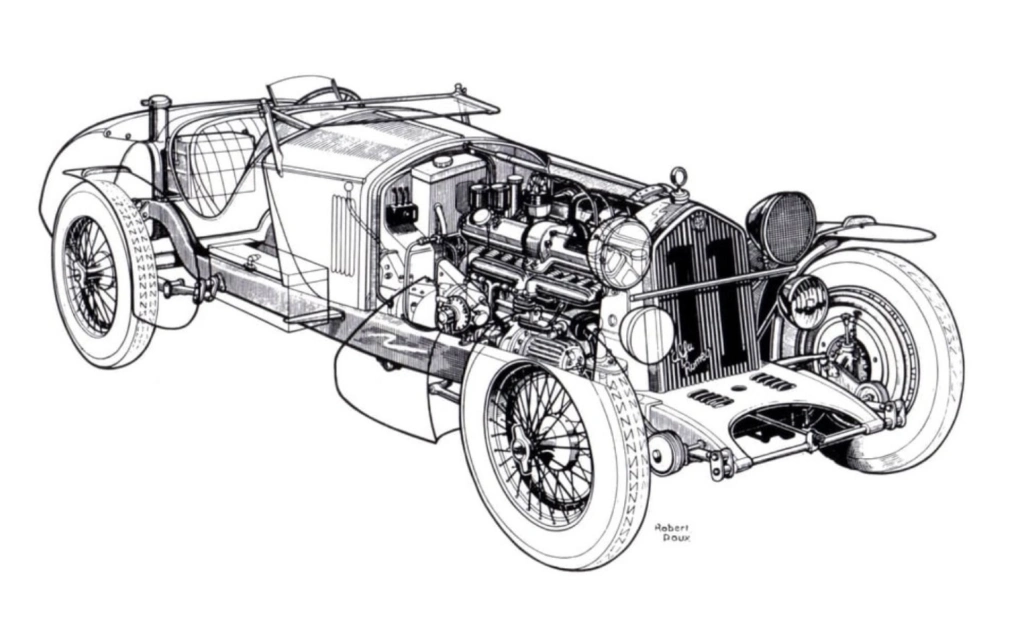
গাড়ির উদ্ভাবন হয়েছিল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সহজে ও দ্রুত চলাচলের মাধ্যম হিসেবে। কিন্তু প্রায় দুই শতাব্দী পর এসে গাড়ি আর শুধু চলাচলের মাধ্যম নেই; বরং গাড়ি পরিণত হয়েছে আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে। নামীদামি ব্র্যান্ডের গাড়ি যেমন বিলাসবহুল, তেমনি নিত্যনতুন প্রযুক্তি গাড়িকে তুলে নিচ্ছে অনন্য উচ্চতায়। তবু কিছু গাড়ি থাকে, যেগুলোর নামের ভারে আশপাশে টেকা মুশকিল। তেমনই কয়েকটি গাড়ির ব্র্যান্ড ও তাদের সূচনালগ্নের গল্প নিয়ে আজকের আলোচনা।
বিএমডব্লিউ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিএমডব্লিউর আত্মপ্রকাশ হয়েছিল যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন তৈরির মাধ্যমে। তখন এর নাম ছিল বিএফডব্লিউ। বিশ্বযুদ্ধ শেষে যুদ্ধবিমান ছেড়ে মোটরযান তৈরি করতে শুরু করে তারা। কিন্তু বিমানের ছায়া সরাতে পারেনি তারা। যে কারণে তাদের লোগোতে এখনো দেখা যায় বিমানের প্রপেলারের ছায়া। বিএমডব্লিউর সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা, তাদের ক্রেতা এবং ক্রেতাদের প্রতি তাদের সমর্থন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে এখন পর্যন্ত তাদের যেকোন গাড়ির পার্টস তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই নতুন করে তৈরি করে পাঠাবে তারা। যে কারণে বিক্রি হওয়া বিএমডব্লিউর বেশির ভাগই এখনো সচল। ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিককে কেন্দ্র করে তারা তৈরি করেছিল বৈদ্যুতিক গাড়ি। যদিও সেটা ছিল প্রদর্শনীর জন্য। মজার ব্যাপার হলো, ১৯৫৯ সালে প্রায় বিক্রি হওয়ার পথে ছিল তারা। তাদের কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল তাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী মার্সিডিজ বেঞ্জ। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে ১৯৯৮ সালে ব্রিটিশ গাড়ি প্রস্তুতকারী কোম্পানি রোলস রয়েসকে কিনে নেয় ভক্সওয়েগন। যাদের মূল প্রস্তুতকারী গাড়ি হলো বিএমডব্লিউ।
টেসলা

গাড়ির দুনিয়ায় টেসলা নিয়ে কথা না বললে কথা যেন অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। মাত্র ২২ বছর বয়সী কোম্পানি যেভাবে গাড়ির বাজারে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। টেসলার মুখ হিসেবে ইলন মাস্ককে দেখা গেলেও এর প্রতিষ্ঠাতা কিংবা উদ্ভাবক কোনোটিই তিনি নন। ২০০৩ সালে মার্টিন এবারহার্ড ও মার্ক টারপেনিংয়ের হাত ধরে শুরু হয় টেলসার যাত্রা। ২০০৪ সালে ইনভেস্টর হিসেবে যোগ দেন মাস্ক, ২০০৮ সালে হন সিইও। শুরু থেকেই পরিবেশ–সচেতন গাড়ি বানানোর ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন তাঁরা। তাঁদের প্রথম গাড়ি রোডস্টার ছিল সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক গাড়ি। সূচনালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত তাদের যতগুলো গাড়ি বের হয়েছে, তার সব কটিই বৈদ্যুতিক গাড়ি।
রোলস রয়েস

গাড়ির জগতে আভিজাত্যের প্রশ্নে সবার আগে আসবে রোলস-রয়েসের কথা। ব্রিটিশ এই গাড়ির নির্মাতা প্রথম নিজেদের গাড়ি তৈরি করে ১৯০৪ সালে। সেখান থেকে এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে অভিজাত গাড়ির তালিকায় শীর্ষ নাম রোলস-রয়েস। চার্লস রোলস ও হেনরি রয়েস নামের দুই ব্রিটিশ নাগরিকের হাত ধরে যাত্রা শুরু করে রোলস-রয়েস। বেশ কয়েকবার মালিকানার বদল হয়েছে, কিন্তু এখনো সেই পুরোনো আভিজাত্য আর জাঁকজমক ধরে রেখেছে রোলস-রয়েস। গুণগত মানের ব্যাপারে এক বিন্দু ছাড় দেওয়া হয় না। যে কারণে রাজা-বাদশাহ থেকে শুরু করে এলিট শ্রেণির পছন্দের তালিকায় থাকে রোলস রয়েস। রোলস রয়েস ঘিরে রয়েছে হাজারও মজাদার গল্প। যেমন তাদের তৈরি ‘ফ্যান্টম ফোর’ মডেলের গাড়ি শুধু রাজবংশীয় হলেই কেনা সম্ভব। আবার গত ১৭ বছরে তৈরি হওয়া প্রতিটি রোলস-রয়েসের পিনস্ট্রাইপ হাতে এঁকেছেন একজন। নিজের মান ও মর্যাদার ব্যাপারে কখনো কার্পণ্য করেনি রোলস রয়েস। যে কারণে ১২১ বছর পর এসেও নিজের আভিজাত্য ধরে রেখেছে রোলস-রয়েস।
মার্সিডিজ-বেঞ্জ

কার্ল বেঞ্জকে ধরা হয় আধুনিক গাড়ির জনক হিসেবে। ১৮৮৬ সালে তিনিই প্রথম গাড়ির ভেতরে কম্বাস্টন ইঞ্জিন প্রবেশ করান। তিন চাকার সেই গাড়িকে ধরা হয় আধুনিক গাড়ির প্রথম ধাপ। সেই গাড়ি চালিয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী বার্থা বেঞ্জ। স্বামীকে না জানিয়ে নিজের সন্তানদের দিয়ে লম্বা পথ পাড়ি দেন বার্থা। সেখান থেকেই যানবাহন হিসেবে গাড়িকে ব্যবহার করা প্রচলিত হতে শুরু করে। ১৯০৬ সালে বেঞ্জ ব্যাটারিচালিত বৈদ্যুতিক গাড়ি আবিষ্কারের চেষ্টাও করেছিলেন। তবে তা কার্যকর হয়নি। গাড়ির দুনিয়ার বেশির ভাগ সেফটি ইস্যু তৈরি হয়েছে মার্সিডিজ-বেঞ্জের হাত ধরে। প্রতিটি গাড়ির ক্র্যাশ সেফটি পরীক্ষা করা, চাকায় সাসপেন্সর যোগ করা, পিন ডোর লক তৈরি করা; সব কটিই প্রথম বাজারে এনেছে মার্সিডিজ-বেঞ্জ। তবে তাদের মার্সিডিজ নাম এসেছে অনেক পরে। শুরুতে তাদের নাম ছিল ডাইমলার মোটোরেন গেসেলশাফট। কার্ল বেঞ্জের সহযোগী গোতিলেব ডাইমলারের মৃত্যুর পর কোম্পানিতে যোগ দেন অস্ট্রিয়ান গাড়ি প্রস্তুতকারী এমিল জেলিনেক। তাঁর মেয়ের নামে গাড়ির কোম্পানির নাম দেওয়া হয় মার্সিডিজ। সঙ্গে বেঞ্জ তো ছিলেনই। শুরুর দিকে তাঁরা জার্মানি ও অস্ট্রিয়ার প্রভাবশালী পরিবারবর্গের কাছে গাড়ি বিক্রি করতেন। ফলে দ্রুতই এটি জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। এখনো সেই জনপ্রিয়তা বজায় আছে।
ল্যাম্বরগিনি

ল্যাম্বরগিনির ইতিহাস লিখতে হলে শুরুতেই নাম নিতে হবে ফেরারির। ইতালীয় গাড়ির কোম্পানি শুরু হয়েছিল ফেরারির তাচ্ছিল্যের মধ্য দিয়ে। ল্যাম্বরগিনির প্রতিষ্ঠাতা ফেরুচ্চিও ল্যাম্বরগিনি ছিলেন একজন ট্রাক্টর নির্মাতা। তাঁর ফেরারি গাড়ি নিয়ে তিনি বেশ অসন্তুষ্ট ছিলেন। গাড়ির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সরাসরি ধরনা দিলেন ফেরারির মালিক এনজো ফেরারির বাসায়। সব শুনে ফেরারি তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, ‘আমাকে গাড়ি বানাতে দাও। তুমি ট্রাক্টর নিয়েই থাকো।’ এনজো ফেরারির মুখে এমন কথা শুনে রাগে ফুঁসে উঠলেন ল্যাম্বরগিনি। গাড়ি করে ফিরতে ফিরতেই সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনিও স্পোর্টস কার বানাবেন, যা শুধু ফেরারিকে ছাড়িয়ে যাবে না, পরিণত হবে বিশ্বের অন্যতম বড় লাক্সারি গাড়ির ব্র্যান্ড হিসেবে। চার মাসের মধ্যে তৈরি করলেন গাড়ির ফ্যাক্টরি, সেখান থেকে তৈরি হলো ল্যাম্বরগিনির প্রথম গাড়ি। ১৯৬৪ সালে ইতালির তুরিনে প্রথম বাজারে এল ল্যাম্বরগিনি ৩৫০ জিটি। প্রথম দিনেই বিক্রি হলো ১৩টি গাড়ি। এর পর থেকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। আস্তে আস্তে ল্যাম্বরগিনি নিজের প্রসার ঘটিয়েছে। বেশ উত্থান–পতনের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পর এখন জার্মান কোম্পানি ভক্সওয়াগন কোম্পানির মালিকানাধীন ল্যাম্বরগিনি। তবে তাদের আইকনিক বাটারফ্লাই ডোরের গাড়ি এখনো সমাদৃত সাধারণ মানুষ ও স্পোর্টস ফ্যানদের কাছে।
টয়োটা

বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে আনাচকানাচে যে গাড়ির দেখা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়, সেটি আর কিছু নয়, টয়োটা। টয়োটা যেন বাংলাদেশিদের সবচেয়ে আপন ব্র্যান্ড। শুরুতে টয়োটা ছিল তাঁত তৈরির কারখানা। সেখান থেকে কিচিরো টয়োটার হাত ধরে শুরু হয় টয়োটা গাড়ির উৎপাদন। আধুনিক দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে টয়োটার জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি। এর পেছনে বড় কারণ টয়োটার গড়ে ওঠা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভঙ্গুর জাপানে চলাচলের জন্য প্রয়োজন ছিল এমন গাড়ির, যা বিশাল ঝক্কিঝামেলা সহজে পাড়ি দিতে পারবে। গ্রামের মেঠো পথ থেকে শহরের আনাচকানাচে ঘুরে বেড়াতে পারবে। সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করে তারা। আস্তে আস্তে জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন হতে লাগল, টয়োটা বাজারে আনল তাদের ‘করোলা’ সিরিজ, যা গাড়ির ইতিহাসে সর্বোচ্চ বিক্রি হওয়া গাড়ির সিরিজ। তাদের করোলা সিরিজের গাড়ি এখনো জনপ্রিয়। ১৯৮৯ সালে বিলাসী গ্রাহকদের আগ্রহী করতে টয়োটা নিজেদের লাক্সারি ব্র্যান্ড হিসেবে তৈরি করেছে লেক্সাস।
ফেরারি

স্পোর্টস গাড়ির দুনিয়ায় যে কটি নাম উচ্চ স্বরে উচ্চারিত হয়, তার একটি হলো ফেরারি। গাড়ির দুনিয়ায় নিত্যনতুন উদ্ভাবন আর প্রযুক্তির মিশেলে ফেরারি থাকবে সবার সামনের সারিতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শুরু হয় ফেরারির যাত্রা। ফেরারির মালিক এনজো ফেরারি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরি করতেন বিমানের যন্ত্রাংশ। যুদ্ধ শেষে তিনি মনোযোগ দেন গাড়ি তৈরিতে, বিশেষ করে স্পোর্টস কার। ১৯৪৭ সালে প্রথম বাজারে আনেন ফেরারি ২৫০ জিটিও। কয়েক বছরের মধ্যে স্পোর্টস ট্র্যাকে ফেরারির জয়জয়কার। ষাট ও সত্তরের দশকে ফেরারির হুইলের পেছনে দেখা গেছে বিশ্বের সেরা রেসারদের। যদিও ষাটের দশকের শেষের দিকে আরেক গাড়ির কোম্পানি ফিয়াতের অধীনে চলে যায় তারা। ২০১৬ সালে ফিয়াত বিক্রি হয়ে গেলে আবারও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ফিরে পায় ফেরারি। বর্তমানে ফেরারি বিশ্বের সেরা স্পোর্টস কারগুলোর মধ্যে একটি। এফ ওয়ান রেসিং–জগতের সেরা তারকা মাইকেল শুমাখার ছিলেন ফেরারির আইকনিক রেসারদের একজন।
ভক্সওয়াগন

জার্মান গাড়ির ব্র্যান্ড ভক্সওয়াগনের যাত্রা শুরু হয়েছিল পিপলস কার হিসেবে। জার্মান লেবার ফ্রন্টের উদ্যোগে সাধারণ মধ্যবিত্ত জনগণের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সূচনা হয় ভক্সওয়াগনের। তখনকার সময়ে সাধারণ মধ্যবিত্ত কারও পক্ষে গাড়ি কেনা ছিল উচ্চাভিলাষী স্বপ্ন। তাদের স্বপ্নকে হাতের মুঠোয় আনতে শুরু হয় ভক্সওয়াগনের যাত্রা। নাৎসি পার্টির প্রধান অ্যাডলফ হিটলার এই কোম্পানির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভক্সওয়াগনের ফ্যাক্টরি মিলিটারি গাড়ি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পথ পরিবর্তন করে তারা, পরিণত হয় গাড়ির দুনিয়ার সবচেয়ে দামি কোম্পানিতে। বর্তমানে বিশ্বের নামী-দামি গাড়ির ব্র্যান্ডের স্বত্বাধিকারী তারা। এর মধ্যে রয়েছে অডি, বুগাতি, পোর্শ, ল্যাম্বরগিনির মতো জায়ান্টরা। কাগজে–কলমে মালিক হলেও তাদের ডিসিশন মেকিংয়ে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেয় না তারা। বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গাড়ি প্রস্তুতকারক ব্র্যান্ড ভক্সওয়াগন।
হুন্দাই

১৯৪৭ সালে হুন্দাই কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি হিসেবে। ২০ বছর পর গাড়ির ব্যবসায় হাত দেয় তারা। ১৯৬৮ সালে প্রথম গাড়ি বাজারে আনে তারা। তাদের কর্টিনা সিরিজের গাড়ি বাজারে এসেছিল ফোর্ডের সহযোগিতায়। তবে নিজেদের গাড়ি বানাতে বেশ সময় লেগেছিল তাদের। ১৯৭৮ সালে প্রথম হুন্দাই পনি ব্র্যান্ডের গাড়ি বাজারে আনে তারা। দক্ষিণ কোরিয়ায় তো বটেই, পুরো বিশ্বে হুন্দাই জনপ্রিয় ব্র্যান্ডদের মধ্যে একটি। টয়োটা ভক্সওয়াগনের পর হুন্দাই বিশ্বের তৃতীয় সর্বাধিক বিক্রীত গাড়ির ব্র্যান্ড।
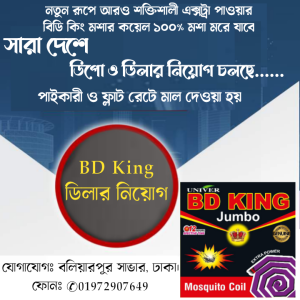
প্রকাশিত সংবাদপত্রের অংশ